স্মরণ
মীজানুর রহমান, সাহিত্য পত্রিকার মহান সাধক
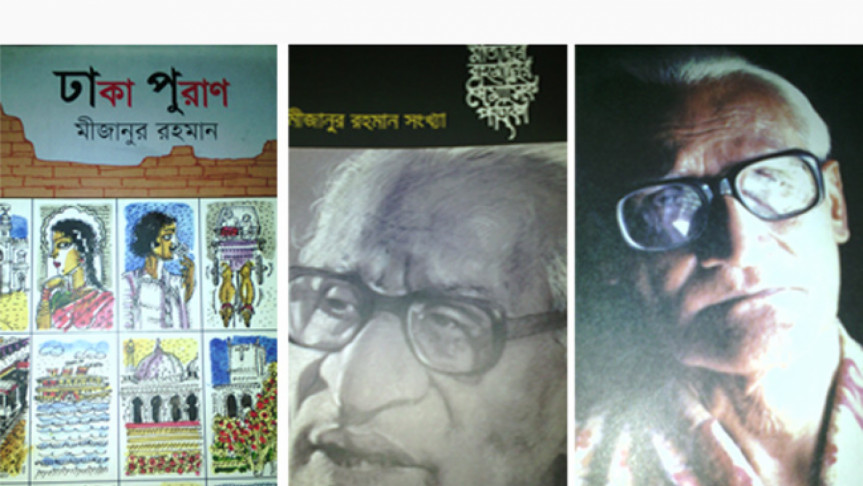
মানুষটির নাম খুব সাধারণ। বানানটা লিখতেন একটু অন্য বৈশিষ্ট্যে। সাধারণত, মিজানুর রহমান লিখতে কেউ মী কার ব্যবহার করেন না। তিনি তাঁর নামটা লিখতেন, ম-এর সঙ্গে দীর্ঘ ই-কার ব্যবহার করে, মীজানুর রহমান। এ দেশে অনেক অনেক মিজানুর রহমান আছেন। কিন্তু কেন একজন মীজানুর রহমানকে উপলক্ষ করে এই নৈবদ্যে সাজানো? কারণ, তিনি মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদক। যাকে কবি শামসুর রাহমান আখ্যা দিয়েছিলেন, সম্পাদকদের সম্পাদক।
হাসিখুশি, প্রাণবন্ত এই মানুষটি জন্মেছিলেন ইছামতি নদীর তীরে বিক্রমপুরের টোল বাসাইল গ্রামে ১৯৩১ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি। তাঁর বাবা ফজলুর রহমান কাজ করতেন কলকাতায়। জন্মের পর বাবার সঙ্গে কলকাতায় গেলেন। ভর্তি হলেন বিখ্যাত মিত্র ইনস্টিটিউটে ১৯৪০ সালে। শৈশব থেকে ধীরস্থির মানুষ মীজানুর রহমান ১৯৪৬ সালেই বের করলেন হাতে লেখা পত্রিকা ‘মুয়াজ্জিন’, কলকাতা থেকেই। বয়স মাত্র নয় বছর।
১৯৪৭ সালে ভয়াবহ দাঙ্গা ও উপমহাদেশ বিভক্তির কালো অধ্যায়ের সময়ে বাবার সঙ্গে চলে এলেন পূর্ব বাংলায়। ভর্তি হলেন আরমানীটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে। পড়াশোনা যাই করেন, মননের গভীরে রোপিত বীজ, পত্রিকা কেবলই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়। তিনিও সাড়া দিলেন। বের হলো ১৯৪৯ সালে মুয়াজ্জিনের পরিবর্তিত রূপ, পূর্ব বাংলার প্রথম কিশোর মাসিক পত্রিকা ‘ঝংকার’। ‘ঝংকার’ পত্রিকায় বাণী দিয়েছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবীবুল্লাহ বাহার, নারীশিক্ষার অগ্রদূত শাসসুননাহার মাহমুদ। ‘ঝংকার’ পত্রিকার লেখক তালিকা দেখলেই বুঝতে পারা যায়, মীজানুর রহমানের দৃষ্টি ও সৃষ্টির করুণাধারা। ঝংকারের লেখকরা ছিলেন জসীমউদদীন, আহসান হাবীব, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, মোহাম্মাদ নাসীর আলী, মবিনউদ্দিন আহমদ, আবদুল্লাহ আল মুতী, ফয়েজ আহমেদ, আশরাফ সিদ্দিকী, হাবীবুর রহমান প্রমুখ। আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর পেছনে ফিরে তাকালে, একজন কিশোরের সৃষ্টিকর্মের উন্মাদনা ও স্বপ্ন কতখানি তীব্র আর জাগরুক হলে, লেখকদের এমন সমাবেশ ঘটাতে পারলেন তাঁর ‘ঝংকার’ পত্রিকায়।
‘ঝংকার’ পত্রিকা বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারেননি তিনি। মাত্র বছর খানেক চলেছিল। ভর্তি হলেন ঢাকা আর্ট কলেজে, এখনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারু ও কলা বিভাগে। এখানে গুরু হিসেবে পেয়েছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, পটুয়া কামরুল হাসান, খাজা শফিক, সফিউদ্দিন আহমেদকে। সতীর্থ হিসেবে পেয়েছিলেন রশীদ চৌধুরী, কাইয়ুম চৌধুরী, বিজন চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, আবদুর রাজ্জাক, খালেদ চৌধুরীদের। কিন্তু বর্ণান্ধতার কারণে চারুকলায় অধ্যয়ন করতে পারেননি। নতুন উদ্যমে শুরু করলেন নতুন অভিধায় নতুন পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা। ১৯৫১ সালে বের করলেন রম্য, সাহিত্য ও বিনোদন পত্রিকা ‘রূপছায়া’। ‘রূপছায়া’ সম্পাদনা করলেন প্রায় ১০ বছর। মীজানুর রহমান সম্পাদিত ও প্রকাশিত রূপছায়া পত্রিকা ছিল তখনকার পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় পত্রিকা। দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা লেখক নায়ক ও নায়িকাদের সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হতো এই পত্রিকায়। তখনকার সময়ের তরুণ অনেক লেখকের লেখা নিয়ে বিজয় দিবস সংখ্যা, প্রেম সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। চিন্তায় ও সৃজনে সব সময়ে মীজানুর রহমান ছিলেন প্রাগ্রসর এবং অবশ্যই আধুনিক।
জীবনের বিচিত্র পথের ভেতর দিয়ে তিনি যাত্রা করেছেন। ১৯৬৫ সালে বেতারে যোগ দেন সহকারী বার্তা সম্পাদক পদে। ১৯৬৭ সালে চাকরি ছেড়ে দিয়ে কথাসাহিত্যিক মাহমুদুল হকের সঙ্গে যৌথভাবে ‘গাঙচিল প্রেস’ প্রতিষ্ঠা করেন ঢাকায়। কিন্তু যাঁদের মননে থাকে শিল্পবোধ, তাঁদের দ্বারা কি ব্যবসা হয়? পরের বছরই গাঙচিল প্রেস বাদ দিয়ে প্রবেশ করেন চাকরিতে। অবজারভার গ্রুপে যোগ দিয়ে বেশ কয়েক বছর চাকরি করার পর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতদ্বৈধতার কারণে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসেন নতুন রূপে নিজের অন্তরভূমিতে, পত্রিকার জগতে।
১৯৮৩ সাল থেকে সম্পাদনা শুরু করলেন ‘মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা’। অভিনব নামে নিজস্ব চিন্তার প্রকরণে পত্রিকা প্রকাশের আগেই অনেকের কপাল কুঁচকে ছিল, নিজের নামে পত্রিকা! লোকটার তো ভারী ইয়ে..। আর পত্রিকাই কেমন হবে? ওসব ভ্রু কুঁচকানো, মুখ বাঁকানোদের দিকে ফিরেও তাকাননি মীজানুর রহমান। তিনি নিজের মতো করে, নিজের রুচি আর সৌন্দর্যে আরোহিত হয়ে একের পর এক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। যাঁরা মুখ কুঁচকে ছিলেন, ভ্রুতে ভাজ রেখেছিলেন, মাত্র কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর তাঁরাই ‘মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা’র পাঠক বনে গেলেন।
এভাবেও লেখা যায়? পাঠক হতে বাধ্য হলেন। কেন তাঁরা পাঠক হতে বাধ্য হলেন? কারণ, ‘মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা’র রুচি, লেখা নির্বাচন এবং সম্পাদনার পরিপাট্য রূপ এ দেশের পাঠকরা আর পায়নি। সোজা কথায়, মীজানুর রহমান সার্থক হলেন। তাঁর সার্থকতার রূপ আরো দৃষ্টিগোচর হলো, নান্দনিকতার চরম পরাকাষ্ঠা অর্জন করল, যখন তিনি পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলো প্রকাশ করতে শুরু করলেন।
শুরুতেই তিনি বিশেষ সংখ্যা সম্পাদনা করলেন ‘কৃষ্ণদয়াল বসু সংখ্যা’। কে এই কৃষ্ণদয়াল বসু? তিনি ছিলেন মিত্র ইনস্টিটিউটের শিক্ষক। যেখানে মীজানুর রহমানের শিক্ষার প্রথম দুয়ার খুলেছিল, সেই শৈশবে, কলকাতায়। এবং কৃষ্ণদয়াল বসু প্রথম বাঙালি, যিনি অনুবাদ করেছিলেন কালিদাসের ‘মেঘদূত’। সংস্কৃতি এবং মননের শিকড় কতটা গভীরে প্রোথিত হলে, হৃদয় মাঝারে নিবেদন থাকলে মীজানুর রহমান ‘কৃষ্ণদয়াল বসু সংখ্যা’ দিয়ে বিশেষ সংখ্যার দরজা খুললেন।
কৃষ্ণদয়াল বসু সংখ্যার পর তিনি সম্পাদনার পরিকল্পনা করলেন ‘আমি কোনো আগন্তুক নই’-এর কবি আহসান হাবীবকে নিয়ে। একে একে সম্পাদনা করলেন শিল্পী রশীদ চৌধুরী সংখ্যা, বৃক্ষ ও পরিবেশ সংখ্যা, কামরুল হাসান সংখ্যা, শামসুর রাহমান সংখ্যা, নদী সংখ্যা, বিদ্যাসাগর সংখ্যা, পক্ষী সংখ্যা এবং সর্বশেষ দুই খণ্ডের গণিত সংখ্যা। গণিত সংখ্যার এক একটি সংখ্যার পৃষ্ঠা সাড়ে সাতশত।
কথায় কথায় মীজানুর রহমান বলতেন, বিশেষ সংখ্যা নিয়ে আমার যে পরিকল্পনা আছে, তাতে আমাকে আরো একশো বছর বাঁচতে হবে। জিজ্ঞাসার উত্তরে বলতেন মাছ সংখ্যা, নাটক সংখ্যা, মুক্তিযুদ্ধ সংখ্যা, নারী সংখ্যাসহ আরো অনেক সংখ্যার পরিকল্পনা আছে আমার। সর্বশেষ যে সংখ্যার কাজ তিনি শুরু করেছিলেন, সেটা বাংলাদেশের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম সংখ্যা। তাঁর খুব খেদ আমাদের দেশে এত বড় একজন বিজ্ঞানী অথচ তাঁকে আমরা যথাযথ মর্যাদা দিচ্ছি না। জাতির পক্ষ থেকে মীজানুর রহমান দায় নিয়েছিলেন, জামাল নজরুল ইসলামকে মর্যাদা দেওয়ার। অনেক লেখাও সংগ্রহ করেছিলেন কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগেই তিনি বিদায় নিলেন ২০০৬ সালের ২৬ জুন কলকাতায়, একটি নার্সিং হোমে।
মীজানুর রহমানের গদ্য লেখার নিজস্ব একটি ঢং ছিল, যা এ দেশের বিদগ্ধজনরা খুব পছন্দ করতেন। প্রতিটি সংখ্যার পেছনের দু-তিন পৃষ্ঠায় নিজের ঢংয়ে লেখা ‘সম্পাদকীয় কড়চা’ লিখতেন। ‘সম্পাদকীয় কড়চা’র ভেতর দিয়ে তাঁর প্রজ্ঞা, তাঁর পরিমিতিবোধ, তাঁর চেতনার আলো, তাঁর মানবিকতার বোধ অনুভব করতাম। তাঁর গদ্য সম্পর্কে জ্ঞানতাপস ওয়াহিদুল হকের মন্তব্য : মীজান অন্যের কাগজে খুব একটা লেখেননি, বইও করেননি বিশেষ কোনো সাম্প্রতিককালের আগে। কিন্তু কী ভাষা, কী ভাব, কী বিষয়! পুরুষানুক্রমে বংশে রক্ষিত মৃগনাভির টুকরোর মতো। নিজের গদ্যভাষা আছে বটে অবনীন্দ্রনাথের যেমন, তেমনি কমলকুমার মজুমদারেরও। ছিল বটে যামিনী রায়ের, সুধীন দত্তের। মীজানের যেন এই ক্ষেত্রের অনন্যতাটিও অনন্যতা। নস্টালজিয়াকে প্রকাশ ও ব্যক্ত করা যথোচিত সংক্রামক করে, এই তাঁর লেখার বড় বিষয়। তাঁর ভাষাটি তিনি তাই যেন বাংলার আবহমানকালের সোঁদামাটি আর বন বাদাড় থেকে সংগ্রহ করেছেন কত যে প্রাকৃত শব্দ, তাদের অধিকাংশের উপস্থিতি নেই অভিধানে।
পরম নিষ্ঠার সঙ্গে, পত্রিকার প্রতিটি লেখা দুই থেকে তিনবার প্রুফ দেখতেন। তাঁর কোনো সহকারী ছিল না, স্ত্রী নূরজাহান বকশী ছাড়া। পত্রিকার যাবতীয় কাজ তিনি নিজেই করতেন। সঙ্গে থাকতেন স্ত্রী, সব সময়ে, ছায়ার মতো। মীজানুর রহমানের ছিল ভয়ংকর হাঁপানি। একেক সময়ে হাঁপানিতে তিনি এতটা কাবু হয়ে যেতেন, দেখে মনে হতো এইবার শেষ। কাশতে কাশতে মানুষটি নুয়ে যেতেন, কিন্তু ইনহেলার টেনে আবার দাঁড়াতেন। মুখের স্নিগ্ধ হাসি দেখে বোঝাই যেত না এই মানুষটি কিছুক্ষণ আগে শরীরের সঙ্গে কী লড়াইটা না করেছেন।
মীজানুর রহমানের দুটি বইয়ের প্রসঙ্গ না তুললেই নয়। তিনি দুটি বইয়ের জনক। প্রথমটির নাম ‘কমলালয়া কলকাতা’। কলকাতায় কেটেছিল তাঁর শৈশবের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো। কালকাতার সেই শৈশব স্মৃতি নিয়ে এমন বর্ণাঢ্য বই খুব কমই লেখা হয়েছে। আদুল গদ্যে, স্মৃতির রোমন্থনে, তীক্ষ্ণ অনুধাবনে এমন বই আর হয় না। বইটি প্রসঙ্গে রাধাপ্রসাদ গুপ্ত লিখেছেন, “এই বইটির সঙ্গে আমি যুক্ত হতে পারছি বলে গর্ববোধ করছি। আমি এই ভূমিকায় কমলালয়া কলকাতার সমালোচনা করতে বসিনি। তবুও বলব যে কলকাতার তিনশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতা নিয়ে যে কটা বই শিক্ষিত রসিকজনের আনন্দের জন্য লেখা হয়েছে, তার মধ্যে শ্রী মীজানুর রহমানের ‘কমলালয়া কলকাতা’ অন্যতম।”
দ্বিতীয় বই ‘কৃষ্ণ ষোলোই’। কেন কৃষ্ণ ষোলো? মানব ইতিহাসের বর্বর হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল ১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকশন আহ্বানের দিন ১৬ আগস্ট উপমহাদেশ জুড়ে। সেদিন কেউ মানুষ ছিল না, ছিল হিন্দু, শিখ নয়তো মুসলমান। মানুষ যখন ধর্মের নামে অন্য ধর্মের মানুষকে হত্যায় মেতে ওঠে, তখন যে হিংস্রর রূপ ধারণ করে, তারই নির্মম পাশবিক বর্ণনায়, একজন প্রত্যক্ষদর্শীর দেখায় লিখেছেন মীজানুর রহমান, তাঁর ‘কৃষ্ণষোলই’ বইয়ে।
মীজানুর রহমান ছিলেন দারুণ স্মৃতিকাতর। তাঁর অধিকাংশ লেখায় স্মৃতিকে তুলে এনেছেন প্রকৃত ধীবরের মতো, শব্দের নিপুণ বুননে। যেমন তিনি শৈশবের কলকাতা নিয়ে লিখেছেন, তেমন লিখেছেন প্রিয় ঢাকা শহরকে নিয়েও।
চমৎকার, নান্দনিক সেই স্মৃতির সম্ভার নিয়ে বের হয়েছে বই ‘ঢাকা পুরাণ’। অনন্যসাধারণ এই বইটি প্রকাশ করেছে একটি খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান।
তার মোহভোগ গদ্যের সামান্য নমুনা উপস্থাপন করছি। তিনি সেইকালের ঢাকা সম্পর্কে লিখেছেন‘ আমাদের নারিন্দার বাড়ি থেকে বন্ধুবর ঔপন্যাসিক মাহমুদুল হক তথা বটুদের মিল ব্যারাকের বাড়ি যেতে হলে সূত্রাপুর ভেঙে লোহার পুল পেরুতেই হতো। এই পুলটা তৈরি হয়েছিল ধোলাইখালের ওপর। সেকালে ঢাকার কালেক্টর ওয়ালটার সাহেবের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে এবং জনগণের সহযোগিতায় ১৮২৩ সালে গড়ে উঠেছিল সম্পূর্ণ পেটা লোহায় তৈরি এই পুল। এর আগে খাল পারাপারে জনগণের বড়ই অসুবিধা হতো। এই অঞ্চলে কোনো বাজার না থাকায় পুলের নিচে একটি বাজার তৈরি করে দেন এই ওয়ালটার সাহেব। বিবি মরিয়মের কামানটি তিনিই প্রথম চকবাজারে স্থাপন করেন, যা পরে সদরঘাট ডিআইটি অ্যাভিনিউ হয়ে এখন জাদুঘরের আঙিনায় শোভা পাচ্ছে। এই ওয়ালটার সাহেবকে আজ আমরা কেউ মনে করি নে, জানিই নে তার সম্বন্ধে কিছু, অথচ ঢাকা শহরের উন্নয়নের মূলে এই ইংরেজ ভদ্রলোকের অবদান বিশাল।
ব্রিটিশ শাসনামলে তিনিই সর্বপ্রথম ঢাকা শহরের উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি ১৮২৩ সালে ঢাকাবাসীদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। পরবর্তীকালে ১৮৬৪ সালে এই কমিটিই ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি নামে অভিহিত হয়।’
তাঁর লেখা ‘ঢাকা পুরাণ’-এ ঢাকা শহরের অসংখ্য দ্রষ্টব্য উঠে এসেছে পরম্পরায়, যা আমরা অনেকেই জানি না। জানার চেষ্টাও করি না।
মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যারগুলোর বিচিত্র বিষয়, বিচিত্র ভাবনা, সম্পাদনার অভিনত্ব, ভাবনার আধুনিকতা, চিন্তার প্রাগ্রসরতা সত্যিই অসাধারণ, বর্ণাঢ্য এবং বিচিত্রতায় পরিপূর্ণ। প্রতিটি সংখ্যার প্রতিটি পৃষ্ঠা নিজে দেখে, সন্তষ্ট হলে ছাপতে দিতেন। দুনিয়ার এমন কোনো বিষয় নেই, যা তিনি জানতেন না। কিন্তু কখনোই ভারাক্রান্ত ছিলেন না। প্রগলভতায় আক্রান্ত হতেন না। সব সময়ে বিনয়ের এক ঐশ্বর্য বুনে চলতেন কথায়, কাজে এবং পত্রিকা সম্পাদনায়।
প্রয়াত হওয়ার পর মীজানুর রহমানের পত্রিকা তাঁকে নিয়ে একটি সংখ্যা প্রকাশ করেছে। এটাও অভিনব। তিনি নেই, কিন্তু তাঁকে নিয়ে তাঁর পত্রিকার একটি সংখ্যা প্রকাশ দুনিয়ায়, এমনটি হয়েছে কি না জানি না। মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকার মীজানুর রহমান সংখ্যায় বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের অনেকে লেখক লিখেছেন, নৈবদ্য জানিয়েছেন, প্রজ্ঞার প্রতি প্রণতি নিবেদন করছেন।
কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন লিখেছেন, ‘এই পত্রিকায় প্রথম গল্প লিখি পক্ষী সংখ্যায়। একটি বিপুল আয়তনের সংখ্যা ছিল এটি। বিস্ময়ে চমকিত হয়েছিলাম। বিজ্ঞাপন বাদে ডবল ডিমাই আকারে ৭৭৮ পৃষ্ঠার এই সংখ্যাটি কেউ প্রকাশ করতে পারে, তা ভেবে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিন্তু মীজানুর রহমানের কাজের বাস্তবতা এমনই ছিল। কত যে বিচিত্র বিষয় ছিল এই সংখ্যায়! পাখিবিষয়ক নানা তথ্য, নানা গল্প, কার্টুন, পাখির রঙিন ছবি, প্রবন্ধ, কবিতা, অনুবাদ, সংকলন, পাখিবিষয়ক বই, ছোটদের পাখির ভুবন ইত্যাদি হরেক রকমের উপকরণ। মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকার পক্ষী সংখ্যা আমাদের সম্পাদনার মানকে হিমালয়ের বেদিতে নিয়ে গেছে।’
মীজানুর রহমান তাঁর কাজ করে গেছেন। আমাদের কাজ বা দায় তাঁকে, তাঁর মতো মহৎপ্রাণ মানুষদের মনে রাখা। তাঁদের রেখে যাওয়া কাজ কাঁধে তুলে এগিয়ে নেওয়া। কিন্তু আমরা কি নিচ্ছি? আমরা গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে দিয়েছি। আমরা আমাদের চারপাশে সর্বনাশের উপাদান দিয়ে দেয়াল নির্মাণ করছি। এই মানুষটি রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো স্বীকৃতি পাননি। কিন্তু রাষ্ট্রের কি কোনো দায় নেই?
মীজানুর রহমানকে এই সময়ের মানুষ চেনে না। জানে না। তাতে কি মীজানুর রহমানের কিছু যায় আসে? তাঁর সম্পাদিত বিশেষ সংখ্যাগুলো আবার যদি পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা যেত! মৃত্যুর ওপারে, মৃত্যুর দেশে মীজান ভাই, বাঙালির যাবতীয় সত্তা নিয়ে নিজের মতো থাকুন, এই কামনা। বড় আনন্দ বেশ কয়েক বছর আপনার অপরিসীম স্নেহ পেয়েছিলাম। সেই স্নেহটুকু আশীর্বাদ নিয়ে বেঁচে আছি। জয়তু মীজানুর রহমান।





















 মনি হায়দার
মনি হায়দার


















